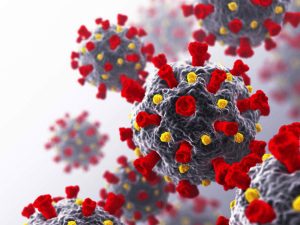– ইঞ্জিনিয়ার একেএম রেজাউল করিম
আমাদের প্রাণের কবি, বিদ্রোহী কবি, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। অগ্রণী বাঙালি কবি, বিংশ শতাব্দীর অন্যতম জনপ্রিয় বাঙালি কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, সংগীতস্রষ্টা, দার্শনিক, যিনি বাংলা কাব্যে অগ্রগামী ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল প্রণোদনার জন্য সর্বাধিক পরিচিত I
আমি একেবারেই ভিন্ন এবং অপ্রিয় একটি বিষয়ের অবতারণা করার চেস্টা করব। আর তাহলো, কবি সাংসারিক জীবনে কি পরিমাণ আর্থিক টানাপোড়েন তথা দারিদ্রতা সহ্য করেছেন। আর এই দারিদ্রতা কবির জীবনে কতটুকু প্রভাব ফেলেছে সেটাও আলোচনায় অবধারিতভাবেই চলে আসবে। আমার মনে হয় বেশীরভাগ মানুষই এমনকি নজরুলভক্তও তাঁর জীবনের এই চরম দুঃখের কথা জানেননা। আর জানলেও কবির জীবনে এর প্রভাব নিয়ে খুব একটা আলোচনা করেন না।অনেকেই আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন এই বলে যে, আর্থিক অসঙ্গতি কি দুঃখের মধ্যে পড়ে। আমি বুঝে শুনেই এটাকে দুঃখ বলেই ধরে নিয়েছি। কারণ আমার মনে হয়েছে এই ‘দুঃখ” কবিকে ভয়ানক পীড়া দিয়েছে, জীবনভর। যাইহোক,
ভূমিকা আর না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় যাওয়া যাক।
এর শুরু জন্ম থেকেইঃ
আমরা সবাই জানি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ডাক নাম ছিল “দুখু মিয়া”। শখ করে কিন্তু এই নামে তাঁকে ডাকা হয়নি। তাঁর শৈশবকালের কঠিন জীবন সংগ্রামের জন্যই তাঁকে এ নামে ডাকা হতো। আর এই নামের মধ্যে দিয়েই তাঁর জীবনের এক কঠিন অধ্যায়কে চিরতরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।
এক দরিদ্র পরিবারে নিতান্ত দুঃখের মধ্যে তিনি মানুষ। তাঁর বাবা ফকির আহমদের দুই স্ত্রী, এবং অনেকগুলো সন্তান-সন্ততি; ফলে সংসার তাঁর পক্ষে একটা মস্তবড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অভাব-অনটনের জ্বালা সেখানে লেগেই থাকত। ফলে মাত্র এগার-বার বছর বয়সের কিশোর কবিকে অন্ন জোটাতে উদয়াস্ত কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। কাজ করতে হয়েছে রুটির দোকানে এবং রাত্রীযাপন করতে হয়েছে ঐ দোকানেরই এক কোনো চিপা জায়গায়; নাম লেখাতে হয়েছে লেটোর দলে। লেটোর দলে যোগদান তাঁর কাব্য–জীবনে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখলেও ইতিহাস সাক্ষী আমাদের বিদ্রোহী কবির এই দারিদ্রের জীবন কখনোই শেষ হয়নি।
পরিণত বয়সেও তিনি দরিদ্রইঃ
সকল বাধা-বিপত্তি সত্তেও কবি সবখানেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হলে।
কবির জীবনে ব্যস্ততা অনেক বেড়ে গেল। একটা সময়ে লেখালেখি করে তাঁর আয়-রোজগার ভালোই হতে লাগলো। কিন্তু বেহিসেবী নজরুলের চাহিদার তুলনায় তা ছিল নিতান্ত সামান্য। সুতরাং সংসারে অভাব অনটন তাঁর পেছন ছাড়লো না।
হুগলিতে থাকাকালীন সময়ে তাঁর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠে এবং তিনি দেনায় জর্জরিত হয়ে পড়েন। পরে সেখান থেকে হেমন্তকুমার নামের এক ব্যক্তির প্রস্তাবে তিনি সপরিবারে কৃষ্ণনগরে চলে আসেন। এখানে এসেও তাঁর আর্থিক দুর্গতি ঘোচেনি। তাঁর অবস্থা ক্রমে ক্রমে এমন দাঁড়াল যে, দিন আর চলে না। কোন কোনদিন উপোস যাওয়ার উপক্রম। কলকাতায় তাঁর যে সব অনুরাগী আছেন, তাদের বিচিত্রা অনুষ্ঠান করে চাঁদা তুলে তাকে সাহায্য করতে হয়েছে। কৃষ্ণনগর থেকে মঈনুদ্দীনের কাছে লেখা কবির একটি চিঠিতে আছে, ‘Variety entertainment- এর কতদূর করলি, জানাবি। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল আমার পক্ষে। কেননা আমার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠছে। আর সপ্তাহখানেকের মধ্যে কি পারবিনে?”
এই দুঃখের পটভূমিতেই ‘দারিদ্র’ কবিতাটি রচিত। বিভিন্ন প্রকাশক, বন্ধু বা শুভাকাংখীদের উদ্দেশ্যে লিখিত কবির অসংখ্য চিঠি পড়লেই দেখা যাবে এগুলোর বেশীরভাগ চিঠিতেই তিনি তাদের কাছে আকুল হয়ে টাকা চেয়েছেন।
যাইহোক, আর্থিক দুরবস্থার দরুন নজরুলের পক্ষে কৃষ্ণনগরে থাকা সম্ভবপর হয়ে উঠল না। তিনি আবার সপরিবারে কলকাতা চলে এলেন। কৃষ্ণনগরে থাকতেই অনেক টাকা তাঁর দেনা হয়েছিল। এককালীন তাঁর বেশ কিছু টাকার প্রয়োজন। ভক্ত ও অনুরাগীরা ‘নজরুল-জয়ন্তী’ করে টাকা যোগারের ব্যবস্থা করলেন।
এই সময়ে তাঁর পুত্র বুলবুল বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। যেখানে তাকে কবর দেয়া হয়েছিল, সে জায়গাটি কিনে রাখা হয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল যে, ভবিষ্যতে কবরটি বাঁধানো হবে। কিন্তু আর্থিক দুর্গতি নজরুলের কোনদিন ঘোচেনি, ফলে কবরটিও বাঁধানো হয়নি। অর্থাভাবের দরুন এইভাবে তাঁর অনেক পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ লাভ করেনি।
পরে তিনি আরো দুইটি সন্তান লাভ করেন। ফলে সংসারে অর্থের চাহিদা তাঁর ক্রমাগত বেড়ে যায় এবং তিনি ভারি বিব্রত হয়ে পড়েন। তাই গানের ব্যবসায়ীরা যখন তাঁর সামনে তুলে ধরল অর্থের থলি, তখন তাঁর পক্ষে তাদের প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয়ে উঠল না। এই সময়ে তিনি শুধু অর্থের জন্য নিয়মিতভাবে গান লিখেছেন মেগাফোন, হিজ মাস্টার্স ভয়েস, নোলা রেকর্ড কোম্পানীর জন্য। অর্থই কাল হয়েছিল তাঁর। বলা যায় অর্থের কাছে বিকিয়ে দিয়েছিলেন নিজেকে। আর এই সময়ে তিনি কিছুদিন টাকার জন্য হা-পিত্যেশ কম করেছেন। কিন্তু বেশীদিন কবির কপালে অর্থের আনাগোনা থাকেনি।
এই সময়ে টাকার প্রয়োজনেই তিনি ছায়াচিত্র ও মঞ্চের সাথেও জড়িত হন। এমনকি ‘ধ্রুব’ চিত্রে তিনি নারদের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এভাবে তিনি অভিনয়, চিত্রনাট্য রচনা, ছায়াচিত্র ও মঞ্চে, সঙ্গীত রচনা ও পরিচালনা করেন। পরে ব্যবসায়ী মনোভাব থেকেই তিনি ১৯৩৪ সালে কলকাতায় ‘কলগীতি’ নামে একটি রেকর্ডের দোকান খোলেন। কিন্তু তিনি জাত ব্যবসায়ী ছিলেন না।
অব্যবসায়ী মনোভাবের কারণে এই দোকান বেশীদিন চলেনি, নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। এবং তিনি আবার দেনায় জড়িয়ে পড়েন। এই সময়ে অনেকের কাছে তিনি টাকা পেতেন। কিন্তু পাওনা টাকা মুখ ফুটে চাইবেন, এমন লোক তিনি নন।
সে এক কঠিন সময়ঃ
১৯৪০ সালে তাঁর স্ত্রী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হলে কবির পারিবারিক জীবনে চরম দুঃখ ঘনিয়ে আসে। রোগ সারাবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেস্টা করতে লাগলেন। টাকার জন্য তিনি তাঁর গাড়ি, (উল্লেখ্য নিতান্ত ঝোঁকের বশে বইয়ের স্বত্ব বিক্রি, গানের রয়্যালটি বাঁধা দিয়ে তিনি একটি গাড়িও কিনেছিলেন)জমি, বইয়ের স্বত্ব, রেকর্ড করা গানের রয়্যালটি বাঁধা য়েছিলেন। কবিরাজী, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথিতে নিরাশ হয়ে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্বিক ক্রিয়াসাধনকেই শ্রেয় বলে মেনে নিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। তাঁর স্ত্রীর অবস্থা বরং দিনে দিনে গুরুতর হতে লাগলো।
এই সময়ে তাঁর আর্থিক সংকট চরমভাবে দেখা দেয়। বিভিন্ন ঋণের দায়ে তিনি একেবারে কোনঠাসা হয়ে পড়েন। এমনকি দেনা শোধের জন্য ইস্টার্ন ইউনিয়ন ব্যাংক তাঁর নামে মামলা পর্যন্ত দায়ের করে। আদালত তখন মাসিক কিস্তিতে ঋণ
পরিশোধ করার হুকুম দেয়। ব্যাংক ঋণের পাশাপাশি তিনি কাবুলিওয়ালাদের কাছ থেকেও ধার করেছিলেন। আগে থেকেই কাবুলিওয়ালা ও অন্যান্য পাওনাদাররা ঋণের টাকা আদায়ের জন্য মাসের শেষের দিকে কবির বাড়িতে হানা দিত। এখন থেকে ব্যাংকের মাসিক কিস্তিও যোগ হলো। সব সময় তিনি কিস্তি পরিশোধ করতে পারতেন না। ফলে সুদ আকারে তা বেড়ে পরের মাসে আরো বড় অংকের টাকার দাবী আসত। ফলে নানামূখী চাপে তিনি একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলেন। এই কঠিন সময়ে তিনি ‘নতুন চাঁদ’ কাব্যের প্রথম সংস্করণ মাত্র আড়াইশ’ টাকায় বিক্রি করে দিলেন। এসব ঘটনা কবির মনে চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো।
এভাবে ঋণের ক্রমাগত চাপ, সংসারের জটিলতা, রোগ-শোক, দুঃখ-বেদনা, আঘাত-অবহেলায় তিনি ধীরে ধীরে মানসিক ভারসাম্য হারালেন এবং অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়লেন। ১৯৪২ সালের ১০ আগস্ট চূড়ান্তভাবে মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত
হওয়ার আগে তাঁর মধ্যে অসুস্থতার লক্ষণ প্রকটিত। কথা বলতে বলতে বা লিখতে লিখতে তিনি ধ্যানস্থ হয়ে পড়তেন। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকতেন।
আর সেই অসুস্থ অবস্থাতেই কবিকে একটি সরকারী চাকরির জন্য তদবির করতে হয়েছে। কবির টাকার বড় প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অসুস্থ বলে শেষ অবধি তিনি চাকরির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হলেন না। এই অবস্থাতেও ‘নবযুগে’ তিনি কাজ
করতেন বটে, কিন্তু তাঁকে ন্যায্য পাওনা মেটানো হয়নি, বরং ঠকানো হয়েছে।
হায়রে মানুষ!!
অসুস্থ হবার পরেও তিনি প্রায় তিন যুগ বেঁচে থাকেন, কিন্তু মৃতের মতো এবং তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভা চিরকালের মতো স্তব্ধ হয়ে যায়। এর মানে হলো, এরপর থেকে আমৃত্যু তাঁকে সাহিত্যকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। আহারে! যাইহোক, নজরুলের আরোগ্যের জন্য গঠিত একটি সংগঠন যার নাম ছিল ‘নজরুল চিকিৎসা কমিটি’ তারা অসুস্থ কবিকে চিকিত্সার জন্য বিলেতে এবং ভিয়েনায় পাঠান। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ অভিমত প্রকাশ করেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে পিক্স ডিজিজ নামক একটি নিউরন ঘটিত সমস্যায় ভুগছেন। এই রোগে আক্রান্তদের মস্তিষের ফ্রন্টাল ও পার্শ্বীয় লোব সংকুচিত হয়ে যায়। তারা আরও জানালেন বর্তমান অবস্থা থেকে কবিকে আরোগ্য করে তোলা অসম্ভব। তখন কবির মাত্র ৪৩-৪৪ বছর; মধ্যবয়স। যথেষ্ট চিকিৎসা সত্ত্বেও নজরুলের স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি।
মহাপ্রয়াণঃ
১৯৭৬ সালে নজরুলের স্বাস্থ্যেরও অবনতি হতে শুরু করে। জীবনের শেষ দিনগুলো কাটে ঢাকার পিজি হাসপাতালে। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নজরুল তার একটি গানে লিখেছেন, “মসজিদেরই কাছে আমায় কবর দিয়ো ভাই/যেন গোরের থেকে মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই”;- কবির এই ইচ্ছার বিষয়টি বিবেচনা করে কবিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে সমাধিস্থ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং সে অনুযায়ী তাঁর সমাধি রচিত হয়।
তাঁর জানাজার নামাযে ১০ হাজারের মত মানুষ অংশ নেয়। জানাজা নামায আদায়ের পর রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, রিয়াল এডমিরাল এম এইচ খান, এয়ার ভাইস মার্শাল এ জি মাহমুদ, মেজর
জেনারেল দস্তগীর জাতীয় পতাকা মন্ডিত নজরুলের মরদেহ বহন করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গনে নিয়ে যান।
বাংলাদেশে তাঁর মৃত্যু উপলক্ষ্যে দুই দিনের রাষ্ট্রীয় শোক দিবস পালিত হয়। আর ভারতের আইনসভায় কবির সম্মানে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অদম্য প্রাণশক্তি নিয়ে জন্ম তাঁর। প্রাণের দুর্বার স্পৃহায়, প্রচন্ড আবেগে, প্রবল উচ্ছ্বাসে তিনি আজীবন তাড়িত ও আবর্তিত হয়েছেন। দারিদ্রকে তিনি ভ্রুকুটি হেনেছেন, অভাব-অনটনকে হাসিমুখে সহ্য করার চেস্টা করেছেন, শত বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে সম্মুখ পানে এগিয়ে গেছেন। সমাজের বাধা-নিষেধ, বিদেশী সরকারের শাসনদন্ড, কারাবাসের নির্মম অত্যাচার, কোনটাই তাঁকে হতদ্যম করতে পারেনি।
শেষের কথাঃ
মাত্র ৪৩-৪৪ বছরের কর্মজীবনে (শুধুমাত্র কবির সুস্থকালীন জীবন-১৮৯৯ থেকে ১৯৪২-৪৩ সাল) তিনি যে সাহিত্যকর্ম রচনা করে গেছেন তা এক কথায় অমূল্য। আমাদের সমাজে একটা কথা প্রায়ই আলোচিত হয়, ‘যদি কবি বাকী জীবন সুস্থ ও
স্বাভাবিকভাবে লিখে যেতে পারতেন তাহলে বাংলা সাহিত্য আরো কত সমৃদ্ধ হত?’
এর উত্তর দেয়া অসম্ভবই বলা যায়। তবে কবির সহজাত রচনাশৈলীর অনন্যসাধারণ দক্ষতা ও প্রতিভা পরিমাপ করে এ কথা সহজেই বলা যায় যে, কবির অসুস্থতা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডী।
আর একটা প্রশ্ন আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। তাহলো, সেই সময়ে কবিকে রক্ষা করার কি কেউ ছিল না? আমি নিজে এ প্রশ্নের উত্তর চাই। কবির বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী কি কেউ ছিল না? খোদাপ্রদত্ত অনন্যসাধারণ প্রতিভার এমন নিভে যাওয়া কি কারো বুকে বাজলো না? এ প্রসঙ্গে কবির কথাই আপনাদের শোনাই,“বন্ধু আমি পেয়েছি যার সাক্ষাত আমি নিজেই করতে পারবো না । এরা সবাই আমার হাসির বন্ধু , গানের বন্ধু, ফুলের সওদার খরিদ্দার এরা। এরা অনেকেই আমার আত্মীয় হয়ে উঠেছে , প্রিয় হয়ে উঠেনি কেউ।“
মাইকেল মধুসূদন দত্তের যেমন বন্ধু বিদ্যাসাগর ছিল তেমনিভাবে কবির জীবনে তেমন বন্ধু আসেনি। আহা! কি যে ভাল হত যদি তেমন বন্ধু তিনি পেতেন! এটা কিছুটা সত্য যে, তিনি বেহিসেবী ছিলেন। জীবন সংসারের জন্য তিনি অতটা বাছ-বিচার করে চলতে শেখেন নি। আর এটাই ত কবির বৈশিস্ট।
১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের আজকের দিনে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কাজী নজরুল ইসলাম।
আজ ২৪শে মে কবির জন্মজয়ন্তী। আমি অতি ক্ষুদ্র মানুষ। কবির মত বর্ণাঢ্য জীবনের একজন মানুষ সম্মন্ধে কিছু লেখার বা বলার সাধ্য আমার নেই। কাজী মোতাহার হোসেন কে লেখা একটি চিঠি আমি পড়েই আমি কিছু একটা লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। সেখানে কবি লিখেছিলেন, “যেদিন চলে যাবো সেদিন হয়তোবা বড় বড় সভা হবে, কত প্রশংসা, কত কবিতা
বেরোবে আমার নামে, দেশপ্রেমিক, ত্যাগী, বীর বিদ্রোহী-বিশেষণের পর বিশেষণ। টেবিল ভেঙে ফেলবে থাপ্পর মেরে-বক্তার পর বক্তা। এই অসুন্দরের শ্রদ্ধা নিবেদনের দিনে তুমি যেন যেয়ো না-যদি পারো চুপটি করে বসে আমার অলিখিত জীবনের কোন একটা কথা স্মরণ করো।”
কবির দুঃখের কথা বলতে বলতে চোখটা মাঝে মাঝেই আদ্র হয়ে উঠছিল। আর বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। শেষ করব কাজী মোতাহার হোসেন কে লেখা কবির ওই চিঠির শেষ অংশ দিয়েইঃ
“…ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে আবার লিখছি। কিন্তু আর লিখতে পারছিনে ভাই। চোখের জল, কলমের কালি দুইই শুকিয়ে গেল। ভালোবাসা নাও।
সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।